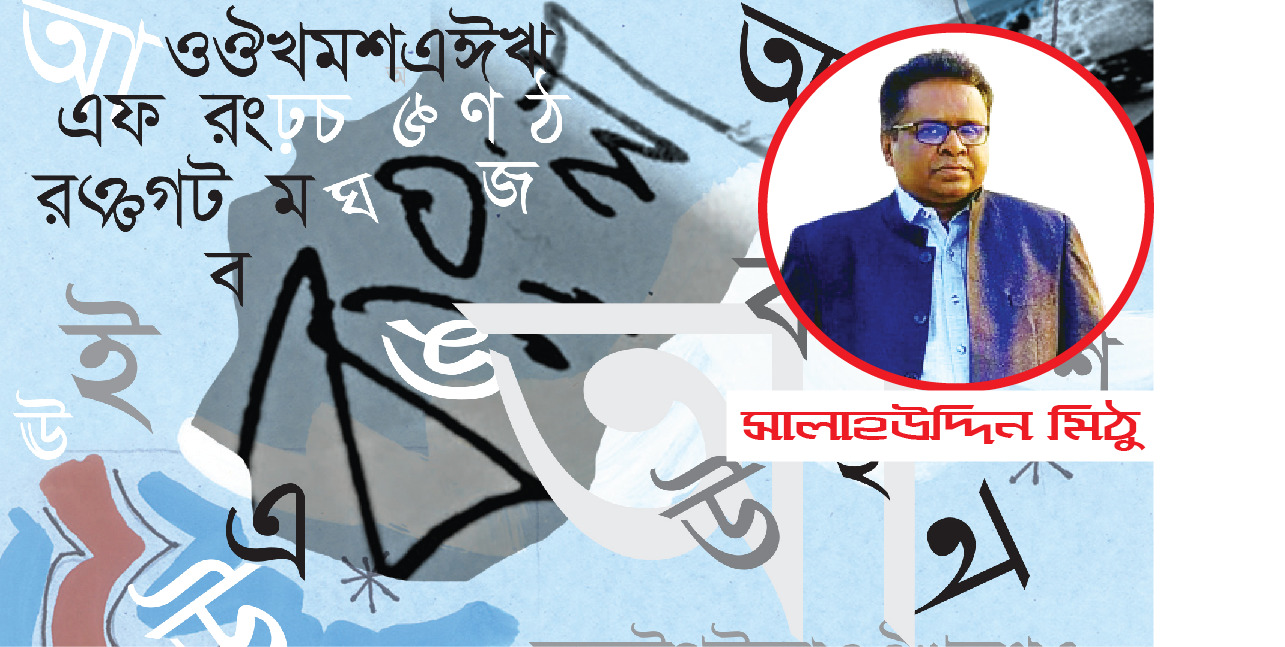সালাহউদ্দিন মিঠু
Published:2025-02-11 13:55:44 BdST
বাংলা ভাষার পটভূমি
“বাংলা ভাষা বিকাশের ইতিহাস ১৩০০ বছর পুরনো। চর্যাপদ এ ভাষার আদি নিদর্শন। অষ্টম শতক থেকে বাংলায় রচিত সাহিত্যের বিশাল ভাণ্ডারের মধ্য দিয়ে অষ্টাদশ শতকের শেষে এসে বাংলা ভাষা তার বর্তমান রূপ পরিগ্রহণ করে। বাংলা ভাষার লিপি হল বাংলা লিপি। বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত বাংলা ভাষার মধ্যে শব্দগত ও উচ্চারণগত সামান্য পার্থক্য রয়েছে। বাংলার নবজাগরণে ও বাংলার সাংস্কৃতিক বিবিধতাকে এক সূত্রে গ্রন্থনে এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশে তথা বাংলাদেশ গঠনে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।
১৯৪৭ থেকে ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দে পূর্ব বাংলায় সংগঠিত বাংলা ভাষা আন্দোলন এই ভাষার সাথে বাঙালি অস্তিত্বের যোগসূত্র স্থাপন করেছে। ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দের ২১শে ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিবাদী ছাত্র ও আন্দোলনকারীরা সংখ্যাগরিষ্ঠের মাতৃভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষাকরণের দাবিতে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেন। ১৯৮৭ সালের বাংলা ভাষা প্রচলন আইন বাংলাদেশের সকল রাষ্ট্রীয় কাজে বাংলার ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।[১৮] ১৯৫২ সালের ভাষা শহিদদের সংগ্রামের স্বীকৃতি স্বরূপ ১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দে ইউনেস্কো ২১শে ফেব্রুয়ারি দিনটিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করে”
বাংলাদেশের অধিবাসীরা প্রথম থেকেই বাংলা ভাষায় কথা বলত না। বাংলা প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষাগোষ্ঠীর অন্যতম ভাষা হিসেবে বিবর্তিত হয়েছে। তাই প্রাক- আর্য যুগের অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় জনগোষ্ঠীর ভাষার সঙ্গে তা সংশ্লিষ্ট নয়। তবে সেসব ভাষার শব্দসম্ভার রয়েছে বাংলা ভাষায়। অনার্যদের তাড়িয়ে আর্যরা এ দেশে বসবাস শুরু করলে তাদেরই আর্যভাষা বিবর্তনের মাধ্যমে ক্রমে ক্রমে বাংলা ভাষার উৎপত্তি হয়েছে।
বাঙালি জাতি যেমন সঙ্কর জনসমষ্টি, বাংলা ভাষাও তেমনি সঙ্কর ভাষা। বর্তমান বাংলা ভাষা প্রচলনের আগে গৌড় ও পুণ্ড্রের লোকেরা অসুর ভাষাভাষী ছিল বলে অষ্টম শতকে রচিত 'আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প' নামক সংস্কৃত গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে। এই অসুর ভাষাভাষী লোকেরা ছিল সমগ্র প্রাচীন বঙ্গের লোক। অসুর ভাষাই অস্ট্রিক বুলি । ড. মুহম্মদ এনামুল হক মন্তব্য করেছেন, ‘বর্তমান বাংলা ভাষা প্রচলিত হইবার পূর্বে আমাদের দেশে যে এই অসুর ভাষা বা অস্ট্রিক বুলি প্রচলিত ছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।' অস্ট্রিক বুলির কিছু শব্দ ও বাকরীতি এখনও বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হয়।
বাংলা ভাষা ইন্দো-ইউরোপীয় মূল ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ মনে করেছেন, আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব পাঁচ হাজার বছর আগে এই মূল ভাষার অস্তিত্ব ছিল । আনুমানিক আড়াই হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দে মূল ভাষা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেসব প্রাচীন শাখার সৃষ্টি হয়, তার অন্যতম হল আর্য শাখা। এ থেকেই ভারতীয় আর্য ভাষার সৃষ্টি। এর কাল ১২০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ।
ভারতীয় আর্য ভাষার তিনটি স্তর :
ভারতীয় আর্যভাষার এই স্তরবিভাগ থেকে দেখা যায় যে, প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার স্তরে বৈদিক ও সংস্কৃত ভাষা প্রচলিত ছিল। জনতার প্রভাবে এ ভাষা পরিবর্তিত হয়ে মধ্যভারতীয় আর্যভাষার স্তরে আসে। প্রথম পর্যায়ে পালি এবং পরে প্রাকৃত ভাষা নামে তা চিহ্নিত হয়। অঞ্চলভেদে প্রাকৃত ভাষা কয়েকটি শ্রেণিতে বিভক্ত হয়ে যায়। এর একটি ছিল মাগধি প্রাকৃত। এ ভাষার প্রাচ্যতর রূপ গৌড়ী প্রাকৃত । তা থেকে গৌড়ী অপভ্রংশের মাধ্যমে বাংলা ভাষার উৎপত্তি হয়েছে। এই পর্যায়ের অন্যান্য ভাষা হল মৈথিলি, মাগধি, ভোজপুরিয়া, আসামি ও উড়িয়া। বাংলা ভাষার জন্মকাল কেউ কেউ দশম শতক বলে নির্ণয় করেছেন।
ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্র মতে বাংলা ভাষার উৎপত্তিকাল খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দী। কম পক্ষে হাজার বছরের পুরানো বাংলা ভাষা উৎপত্তির পর থেকে নানা পর্যায়ে পরিবর্তনের মাধ্যমে আধুনিক পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। বাংলা ভাষার বিবর্তনের ইতিহাসে আদি মধ্য ও আধুনিক—এই তিন যুগের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করা যায়। আদি বা প্রাচীন যুগের বাংলা ভাষার কাল দ্বাদশ শতক পর্যন্ত বিস্তৃত। এ সময়ের প্রধান নিদর্শন চর্যাপদ। এর ভাষা থেকে তখন পর্যন্ত তার পূর্ববর্তী অপভ্রংশের প্রভাব দূর হয়ে যায় নি, এমন কি প্রাকৃতের প্রভাবও তাতে বর্তমান ছিল। তবে এখানেই বাংলা ভাষা তার স্বতন্ত্র মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়েছে।
বাংলা সাহিত্যের ছাত্র-ছাত্রীরা আরও ভালো বলতে পারবে হয়তো, তবে বাংলা সাহিত্যে ফার্সী শব্দের প্রভাব পরতে শুরু করে মুঘল শাসনামলে, ষষ্টদশ শতকের মাঝামাঝি থেকে বাংলা ভাষায় অন্যান্য বিদেশী ভাষার ছাপ পরতে শুরু করে, লোকের জবান থেকে কবিতার পঙক্তিতে উঠে আসে সেসব বিদেশী শব্দ, পরবর্তীতে বাংলা গদ্যের সূচনার ইতিহাস লিখতে গিয়ে গোলাম মুরশিদ লিখেছেন বাংলা ভাষায় প্রচলিত গদ্যে আরবি-ফার্সী শব্দের পরিমাণ ১৫ শতাংশ ছিলো। আলালী ভাষা সম্ভবত কোলকাতার তৎকালীন সময়ের প্রচলিত ভাষার প্রতিনিধিত্ব করে না, সেখানে আরবি ফার্সী শব্দের শতকরা অনুপাত অনেক বেশী।
ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের জন্ম হয়েছিলো ইংরেজ প্রশাসকদের দেশীয় ভাষা শেখানো এবং আরও দক্ষ ভাবে প্রশাসন পরিচালনার প্রশিক্ষণের প্রয়োজনে। সেখানে উপযুক্ত বাংলা ভাষা শেখানোর শিক্ষক খুঁজে পান নি কলেজ পরিচালকগণ। উইলিয়াম কেরী যে সময়ে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সাথে সম্পর্কিত হলেন তার আগেই বাংলা গদ্য দিক পরিবর্তন করেছে, উইলিয়াম কেরীর প্রথম দিকের অর্থ্যাৎ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ পূর্ববর্তী গদ্য রচনা এবং পরবর্তী সময়ের গদ্য রচনায় শব্দ চয়নের ধরণ অনুসরণ করলেই বুঝা যায় উইলিয়াম কেরী প্রচলিত বাংলা ভাষার বিপরীতে গিয়ে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রভাবে নিজের লেখ্য গদ্য ভাষার পরিবর্তন করেছেন এবং তিনি পরবর্তীতে সংস্কৃতকে বাংলা ভাষার জননী হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন।
বাংলা গদ্যের সাহেবীয়ানা এবং ইন্দো-ইরানিয় ভাষার সাথে ইউরোপের ভষার সাদৃশ্য খুঁজে মুগ্ধ পাদ্রীদের নিজস্ব খেয়ালে তারা সংস্কৃতকে বাংলা ভাষার জননী বানিয়েছিলেন, আর্য ভাষা বাংলা ভাষার আদিম পর্যায় নয় সেটা কয়েকজন মৃদু কণ্ঠে বলতে চাইলেও তাদের ক্ষিণকণ্ঠ জনপ্রিয় মতবাদের উচ্চস্বরে হারিয়ে গিয়েছিলো।
ইংরেজ শাসকদের বাংলা ভাষাপ্রীতি নিছকই প্রশাসনিক প্রয়োজন, বাংলা ভাষায় আইনের ভাষ্য রচনার তাগিদ মূলত ফার্সীকে হটিয়ে ইংরেজী এবং স্থানীয় ভাষাকে প্রশাসনিক ভাষা করে তুলবার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা। সে উদ্যোগ থেকেও পরবর্তীতে ইংরেজ প্রশাসকগণ পিছিয়ে এসেছেন এবং অর্ধ শতাব্দী পরে ইংরেজীকেই প্রশাসনিক ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। বৌদ্ধ শাসকদের হটিয়ে যখন হিন্দু শাসকেরা বাংলার প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা শুরু করেন তারাও একই ভাবে স্থানীয় ভাষাকে বাদ দিয়ে সংস্কৃতকেই প্রশাসনিক ভাষা কিংবা দাপ্তরিক ভাষার মর্যাদা দিয়েছিলেন, লক্ষণ সেন নিজগৃহে স্থানীয় ভাষায় বাক্যালাপ করলেও দাপ্তরিক কাজে সংস্কৃত ব্যবহার করেছেন।
স্বাধীন নবাবগণ বাংলার মসনদ দখল করে স্থানীয় ভাষাকে দাপ্তরিক ভাষা করেছিলেন, ফলে বাংলা সাহিত্যের পৃষ্টপোষক হিসেবে তারা নন্দিত হয়েছেন। মুঘলগণ প্রশাসনিক কাজে ফার্সী ভাষার ব্যবহার শুরু করেছিলেন স্থানীয় ভাষাকে হটিয়ে এবং ইংরেজগণ পুনরায় স্থানীয় ভাষাকে প্রশাসনিক ভাষার মর্যাদা দিয়েছেন।
ইংরেজগণ যখন সকল বিজ্ঞপ্তি ও আইনের ভাষ্যের অনুবাদ করছেন সে সময়ে কয়েকজন মুসলমান অনুবাদক হিসেবে কাজ করলেও পরবর্তীতে অনুবাদের দায়িত্ব গিয়ে বর্তায় বৃন্দাবন, নদীয়া এবং অন্যান্য টোল থেকে পড়ে আসা সংস্কৃতবিজ্ঞ অনুবাদকদের স্কন্ধে, তাদের সাথে তাল মিলয়ে ভুল সংস্কৃতে অনুবাদ করেছেন কেরী সাহেবের মুন্সী।
বৃন্দাবন ও নদীয়ার টোলপ্রত্যাগত সাহিত্যিক বামুনগণ সাহেবদের উৎসাহেই প্রচলিত বাংলা ভাষার বদলে সংস্কৃত শব্দের প্রতি অধিক আনুগত্য প্রকাশ করতে চেয়ে বাংলা ভাষার স্বাভাবিক বিবর্তনের ধারায় রাশ টেনে ধরেছিলেন।
পরবর্তীতে সাহেবানুগত বাংগালী ভাষাতাত্ত্বিকেরাও একই ভাবে সংস্কৃতের আনুগত্য মেনে চলেছেন, জোরপূর্বক যেকোনো শব্দের উৎসে সংস্কৃত আনতে গিয়ে কল্পনার ডানা অযথার্থ বিস্তার করে যেকোনো উপায়েই নিয়ম না মেনেই নিজের মতো উৎস তৈরি করেছেন।
এই প্রক্রিয়ায় বাংলা ভাষার স্বাভাবিক বিকাশ ব্যহত হয়েছে, ভাষার শক্তি অন্য ভাষার শব্দ আত্মস্যাৎ করার ক্ষমতা এবং অন্যান্য উৎসব্যতিরকে নিজ উদ্যোগে শব্দ উৎপাদনের ক্ষমতা। এভাবেই ভাষা বিকশিত হয়, ভাষার শব্দসম্ভার বৃদ্ধি পায়, ভাষার প্রকাশ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, পুরোনো আর্য ভাষা প্রচুর দেশী শব্দ আত্মস্যাৎ করে নিজেকে বিকশিত করেছে, মুন্ডা, কোল, এবং অন্যান্য উৎস থেকে সংস্কৃতের উদরে ঢুকে যাওয়া শব্দগুলো পুনরায় সংস্কৃতের মাধ্যমে বাংলা ভাষায় প্রত্যাগমণ করেছে।
কিন্তু সংস্কৃতরীতির প্রতি অন্যানয় মুখাপেক্ষিতা বাংলা ভাষার স্বাভাবিক শব্দ আত্মস্যাৎ প্রক্রিয়া এবং নতুন শব্দ উৎপাদন ক্ষমতাকে সীমিত করেছে। নতুন নতুন ভাবনা প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা সংস্কৃতের মতো মৃত ভাষা পুরণ করতে পারে নি। আমাদের জ্ঞানচর্চায় গুরুতর সীমাবদ্ধতা তৈরি করেছে এই সংস্কৃতমুখাপেক্ষিতা।
সেই সংস্কৃতায়নের বিপরীতে একেবারে দেশজপ্রতিক্রিয়ায় হিন্দী-উর্দু শব্দে জেরবার পূঁথি সাহিত্য, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ জন্মের কাছাকাছি সময়ে পূঁথি সাহিত্য বিকশিত হতে শুরু করেছে, সৈয়দ হামজার জন্ম ১৭৩৩ খ্রীস্টাব্দে, ইংরেজগণ ফার্সীর বদলে দেশী ভাষায় দাপ্তরিক কর্মকান্ড শুরু করেছেন ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দের পরবর্তী সময়ে, তারও কয়েক বছর পরে সৈয়দ হামজা গরীবুল্লাহ’র সংস্পর্শ্বে আসেন, গরীবুল্লাহ তখন আমীর হামজা পূঁথি রচনা করছেন, তিনি আমীর হামজা সমাপ্ত করে যেতে পারেন নি, সৈয়দ হামজা সে পূঁথি সমাপ্ত করেন।
পূঁথি রচনার ঐতিহ্য দুই শতকের, এমন কি বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধেও বাংলা ভাষায় পূঁথি রচিত হয়েছে।সে ধারায় ভবিষ্যতের হিন্দু মুসলমান ব্যবধানের বীজও সুপ্ত ছিলো, সংস্কৃতপ্রেমিক সাহিত্যিকদের নিজস্ব সংস্কৃতঅনুগামী বাংলা সাহিত্যের ধারা নির্মাণের সাথে সাথে মুসলমানদের ভেতরেও এরই প্রতিক্রিয়ায় অধিক পরিমাণে মুসলমানী শব্দসম্বলিত সাহিত্য রচনা, ধর্মীয় বয়ান রচনার উৎসাহ প্রকট হয়ে উঠে। সেসব উন্মাদনের একটা ধারা পাকিস্তান আন্দোলনকে বলবান করে, পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম এদেশের কয়েকজন সাহিত্যিকের ক্ষমতাকে একেবারে ধ্বংস করে দিয়েছে, পাকিস্তানের ঐতিহ্য এবং সাধারণ মুসলমান জাতীয়তাবাদের প্রতি ভক্তি থেকে তারা মুসলমানী বাংলায় সাহিত্য চর্চা করে নিজের সাহিত্যিক অপমৃত্যু ডেকে এনেছেন, ব্যতিক্রম আবুল মনসুর আহমেদ, তার মুসলমানী গদ্য সুখপাঠ্য। এদের কয়েকজনের নিজস্ব ক্ষমতা ছিলো না, কিন্তু ফররুখ আহমেদ নিজের স্বাধীন সিদ্ধানের বলী বলেই মনে হয় আমার।
স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় আমাদের বাংলা ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদ বিকশিত হয়েছে, তারই অনুপ্রেরণায় বাংলা সাহিত্য চর্চা বৃদ্ধি পেয়েছিলো, দীর্ঘ অভ্যাসে অভ্যস্ত হয়ে যাওয়া শব্দগুলোর সাথে সংস্কৃত শব্দ ব্যবহারকেও দুষণীয় মনে হয় নি তখন।
তীব্র হিন্দু বিদ্বেষ কিংবা কোলকাতাবিদ্বেষ কিংবা নিজের সার্বভৌমত্ব ও জাতীয়তাবাদের প্রতি অযাচিত ভক্তি কিংবা অন্য যেকোনো কারণেই হোক না কেনো বাংলাদেশে মুসলমান গদ্যের প্রতি অনুরক্ততা বেড়েছে। এখন বাংলাদেশেই হবে বাংলা সাহিত্যের তীর্থ এমন আকাঙ্খা থেকে একদল মানুষ বাংলা ভাষার ঐতিহ্যবিচ্যুত হয়ে মুসলমানি বাংলা গদ্যের পুনপ্রচলন আন্দোলনে লিপ্ত।
এখন বাংলাদেশে সে ধারার অনুসরন করছেন একদল আবাল, তা্দরে বাংলা ভাষার সুন্নতে খৎনার পৌরোহিত্য করছেন যে ভদ্রলোক তিনি আবার সাধু বাংলায় লিখেন এবং যিনি মূল গায়েন তিনি কোনো অদ্ভুত বিবেচনা থেকে প্রতিনয়ত নিজের ঘাট বদল করে এখন এইসব আবালদের রসুলত্ব গ্রহন করেছেন।
Unauthorized use or reproduction of The Finance Today content for commercial purposes is strictly prohibited.